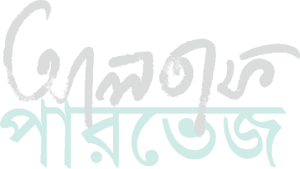কিছুদিন আগে গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভ্রাম্যমান করোনা সেবা উদ্যোগ নিয়ে লেখার পর কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী কেন অনেকের অপছন্দের? তিনি ওষুধ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে অতীতে কী করতে চেয়েছিলেন?
বিষয়টি পৃথকভাবে আলোচনার দাবি রাখে। সেজন্যই আলাদা করে এই আলাপের উদ্যোগ। এই আলাপ অতি সংক্ষিপ্ত। একে যারা পূর্ণাঙ্গ করতে চান তারা অংশ নিতে পারেন। সেটা জরুরিও। এখানে যেসব তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো জাফরুল্লা চৌধুরীর পুরানো লেখনি থেকে নেয়া। এর সত্যা-সত্য নিয়ে প্রশ্ন থাকলে এবং ভিন্নমত থাকলেও অবশ্যই লিখবেন।
করোনার বিরুদ্ধে এই দীর্ঘযুদ্ধে বেঁচেমরে শেষপর্যন্ত যে কয়জন জিতবে এদেশে– তাদের অবশ্যই ওষুধ ও স্বাস্থ্য প্রশ্নে নতুন করে ভাবতে হবে। তখন এসব নিয়ে অতীতের সংগ্রামের কথা আসবে। অসমাপ্ত সেই সংগ্রামের শিক্ষা তখন কাজে লাগতে পারে। এটা কেবল একজন জাফরুল্লাহ চৌধুরীর একার ব্যাপার না।
*
গণস্বাস্থ্য ফার্মা এবং গণস্বাস্থ্য হাসপাতাল দু’বার ভাঙচুরের শিকার হয়। প্রথমবার এটিতে আগুন দেয়ার চেষ্টা হয় ১৯৮৪ সালের আগস্টে; দ্বিতীয়বার ১৯৯০-এর অক্টোবরে। গণস্বাস্থ্য ও ডা. জাফরুল্লাহ প্রথমবার আক্রান্ত হয় ওষুধ-নীতি নিয়ে। দ্বিতীয়বার স্বাস্থ্য-নীতি নিয়ে। দুটো ঘটনায় প্রবল যোগসূত্র আছে। আমরা ওষুধ-নীতির অধ্যায় থেকে শুরু করতে পারি।
*
মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই দেশের স্বাস্থ্যখাত এবং ওষুধ নিয়ে নতুন ভাবনা শুরু হয়েছিল। বিশাল গ্রামবাংলায় কীভাবে স্বাস্থ্যসেবাকে সঠিকভাবে এগিয়ে নেয়া যায় সেটা যুদ্ধোত্তর সমাজেরই একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। বিশেষ করে সেই সব চিকিৎসক এটা তীব্রভাবে ভাবতেন যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ‘মুক্তি’ বিষয়টিকে এরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি খাতেও সম্প্রসারণ করতে তৎপর ছিল।
এসময় দেশটিতে স্বাস্থ্যখাতের অবস্থা ছিল করুণ। প্রতি এক হাজার নবজাতকের ২৬০ জন ৫ বছরের মধ্যে মারা যেত। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ পাওয়া দুরূহ হতো। দামও ছিল অযৌক্তিকভাবে বেশি। ওষুধের ব্যবসার প্রধান সুবিধাভোগী ছিল বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। সরকার এসময় টিসিবির মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশ থেকে ওষুধ আমদানি শুরু করে। এতে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যসহ অনেকে অসন্তুষ্ট ছিল। তাতে সেটাও কমাতে হয়। ফলে ওষুধ খাতে বহুজাতিকদের একচেটিয়াত্ব বাড়তেই থাকে।
১৯৭৮ নাগাদ দেশে একটা ওষুধ নীতির খসড়া তৈরির কাজ শুরু হয়। এসময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন ড. এম এম হক। খসড়া অবস্থাতেই ওই ওষুধ নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় ‘ওষুধ শিল্প সমিতি’। তাদের প্রতিবাদে ওটা খসড়াতেই থেমে যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদ হারান। এ কাজে তখনকার একজন মন্ত্রীরও ইন্ধন ছিল।
বাংলাদেশে অনেকেই বলেন ওষুধ নীতি জেনারেল এরশাদের অবদান তা কিন্তু ঠিক নয়। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই জের।
*
১৯৮২ সালে এসে ২৮ এপ্রিল ওষুধ-নীতি তৈরি করতে ৮ সদস্যের একটা কমিটি হয়। এই কমিটিতে কোন আমলা ছিল না। সবাই ছিল চিকিৎসাবিদ্যার লোক। যার প্রধান ছিলেন পিজির অধ্যাপক নূরুল ইসলাম সাহেব। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন মাত্র। এই কমিটির অধিকাংশ সদস্য বিএমএ’র সদস্যও ছিলেন।
এই কমিটি অনেকগুলো বৈঠক শেষে ১৬টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেশের ওষুধ খাত নিয়ে তদন্তে নামে। দেশে এসময় ওষুধ তৈরির জন্য ১৭৭টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ছিল। পাশাপাশি প্রচুর বিদেশী ওষুধ আমদানি হতো। কমিটি প্রায় ৪ হাজার ধরনের ওষুধের সন্ধান পায়। দেখা যায়, এতো বিভিন্ন নামের ওষুধ আসলে ১৫০টি উপাদানে তৈরি ওষুধেরই রকমারি কোম্পানি নাম মাত্র।
১৬টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে এসব ওষুধ পরীক্ষা শেষে নূরুল ইসলাম কমিটি ১ হাজার ৭৪২টি ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় বা অকার্যকর ওষুধ শনাক্ত করে। এর মাঝে প্রায় ৯০০ ওষুধ তারা বাজার থেকে বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে তুলে নেয়ার সুপারিশ করে। পাশাপাশি ‘অত্যাবশ্যকীয় ওষুধে’র একটা তালিকা করা হয়। এই কমিটির বড় অবদান ছিল
: ওষুধের মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালী করার সুপারিশ;
: বাংলাদেশে কারখানা না করে থার্ড পার্টির মাধ্যমে ওষুধ উৎপাদনে বিদেশী কোম্পানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ;
: দেশে থাকলে বিদেশ থেকে ওষুধের কাঁচামাল আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং বিদেশ থেকে ওষুধের কাঁচামাল আমদানিকে প্রতিযোগিতামূলক করা;
: আয়ুর্বেদী ও ইউনানি ওষুধকে আইনের আওতায় আনা;
: ৪৫টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধকে পর্যায়ক্রমে জিনেরিক নামে বাজারজাত করা। আগে একই এমপিসিলিন ৪৮টি কোম্পানি ৪৮ নামে বাজারজাত করতো। আলাদা ব্র্যান্ড নাম হওয়ায় সাধারণ ক্রেতা অনেক ব্র্যান্ডে দামের ক্ষেত্রে প্রতারিত হতো।
১৯৮২ সালের ২৯ মে মন্ত্রীসভা এসব সুপারিশ অনুমোদন করে। ১২ জুন সেটা ‘ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ’ নামে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি হয়।
তৃতীয় বিশ্বের স্বাস্থ্যখাতের জন্য এটা ছিল এক অভাবনীয় দৃষ্টান্ত। বহুজাতিকরা এতদিন নিজেদের চ্যালেঞ্জ অযোগ্য ভাবতো। সেখানে এই প্রথম একটা ঘা লাগে।
*
পাল্টা ঝড় উঠতেও দেরি হলো না। ১ জুনই যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেনারেল এরশাদের সঙ্গে দেখা করেন। ওষুধকে ঘিরে দেশ-বিদেশে রাজনীতির পুরো চেহারাটি আস্তে আস্তে এসময় বাংলাদেশে উদোম হতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি জার্মানি, ডাচ ও ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতও সরকারের উপর সম্মিলিত চাপ দেন ওষুধ নীতি বদলাতে।
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিসেস কুনকে এসময় বাংলাদেশের প্রভাবশালী দৈনিকের সম্পাদক এবং বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘনঘন বৈঠক করতে দেখা যায়। ঢাকার টিকাটুলি থেকে প্রকাশিত প্রভাবশালী একটা বাংলা এবং একটা ইংরেজি দৈনিক এসময় ওষুধ নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। জুনেই জেনারেল এরশাদকে যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি যদিও এটা আইনে পরিণত করেই ওয়াশিংটন গেলেন– কিন্তু সেখানে যেয়ে কথা দিয়ে এলেন যে আইনটি রিভিউ করা হবে।
*
ওষুধ-নীতি বাস্তবায়ন হলে বিদেশী বিনিয়োগ চলে যাবে এবং বহু ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে এমন একটা প্রচারণা চলতে থাকে তুমুল বেগে এসময়।
বিদেশী এই চাপ প্রয়োগের মূল কারণ ছিল বাংলাদেশের এই ওষুধ নীতি সফল হয়ে গেলে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে একই রকম নীতির জন্য রাজনৈতিক রূপান্তরবাদীরা চাপ প্রয়োগ শুরু করবে।
বাংলাদেশের ওষুধ বিষয় কীভাবে আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের মাথাব্যথার কারণ হয়েছে এ নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টে রিপোর্ট হয় ১৯৮২ সালের ১৯ আগস্ট। শিরোনাম ছিল: ‘ইউএস ইজ এইডিং ড্রাগ কোম্পানিজ ইন বাংলাদেশ’।
ক্রমাগত চাপ ও তদবিরে মাধ্যমে মূল ড্রাগ পলিসি এরপর অনেকখানি পাল্টে যায়। প্রথম ‘রিভিউ’ হয় ১৯৮২-এর ৭ সেপ্টেম্বর। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ আরো সংশোধিত হয়।
*
ওষুধ নীতি নিয়ে বিতর্ককালের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক ছিল কোম্পানিগুলোর পাল্টা প্রচারণা এবং তাতে দেশের চিকিৎসক সমাজের সংহতিতে ঢাকার মধ্যবিত্তরা সাধারণভাবে ওষুধ নীতির বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছিল।
এখানকার মধ্যবিত্তরা যেকোন বড় ধরনের রূপান্তর উদ্যোগে যে কীভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা রাখতে পারে তার একটা মহড়া হয়ে যায় ওষুধ নীতির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানে। একই ঘটনা দেখা যায় কয়েক বছর পর স্বাস্থ্য-নীতির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানেও।
বলা বাহুল্য, জেনারেল এরশাদের সরকার দেশ-বিদেশের এসব মহলের বিরুদ্ধে দীর্ঘযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মতো সরকার ছিল না। ফলে দ্রুতই ওষুধ নীতিতে সংশোধন ঘটতে থাকে। পরবর্তীকালের এরকম নির্বাহী আদেশের ফল হিসেবে খুব কম সংখ্যক ওষুধই আর মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকে। তারপরও ওষুধ-নীতির এমন কিছু সুফল অবশিষ্ট ছিল যার মাধ্যমে দেশের ওষুধ-শিল্প অনেক বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে বাংলাদেশ ওষুধ রফতানিকারক দেশে পরিণত হয়। কিন্তু এসব বিকাশ থেকে ভোক্তা হিসেবে রোগীরা প্রত্যাশিত মাত্রায় সুবিধা পায়নি।
ওষুধ নীতির এই ইতিহাসের মাঝেই ১৯৮৩-এর জুলাইয়ে দেশের চিকিৎসা পেশার নেতৃত্বস্থানীয় ৬৩ জন ব্যক্তি বিএমএকে অনুরোধ করে প্রফেসর নূরুল ইসলাম ও ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য।
এসময় জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিশেষ রাগ ছিল কয়েকটি কারণে। যেসব চিকিৎসক স্বাধীনতা-যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও ওষুধ খাতে আমূল পরিবর্তনের জন্য লড়ছিলেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় একজন। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে ওষুধের কাঁচামাল এবং ওষুধের দাম সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত, বহুজাতিকদের ব্যবসায়িক চাতুরি সম্পর্কিত তথ্যাদি গণস্বাস্থ্যের মাধ্যমে দেশে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নেন তিনি। সরকারকেও তিনি এসব তথ্য এনে দিতেন। তৃতীয়ত জনস্বাস্থ্য নিয়ে বিদেশে যারা কাজ করছে এমন একটিভিস্টদেরও তিনি বাংলাদেশের ওষুধ-নীতির লড়াইয়ে কাজে লাগাচ্ছিলেন।
তাঁর কাছে এটা ছিল বৈশ্বিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের একটা রাজনৈতিক কাজ। বাংলাদেশের ‘র্যাডিক্যাল’দের তরফ থেকে তিনি সেসময় ভালো সংহতি পাননি। বরং তখন এমনও প্রচার চালানো হয়, ‘জাফরুল্লাহ খ্রিস্টানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটা মুসলমান দেশের ওষুধ শিল্প ধ্বংসে নেমেছেন। এতে বাংলাদেশ ভারতীয় ওষুধের বাজারে পরিণত হবে।’ তাঁর বিচার চেয়ে অজ্ঞাত উৎস থেকে পোস্টার লাগানো হয় দেয়ালে দেয়ালে।
ওষুধ-নীতির বিরুদ্ধে এরকম অবিশ্বাস্য মাত্রার প্রচার-প্রচারণা রুখতে এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতেই এক সময় ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য’ নামে একটা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ওষুধ তৈরিকারী কোম্পনিগুলোর বিজ্ঞাপনের যে চাপ ও কার্যকারিতা আজও বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমে এবং ভোক্তাদের মনোজগতে প্রভাব বিস্তার করে আছে তাতে স্বাস্থ্য খাতে ভোক্তা-বান্ধব পুনর্গঠন প্রকৃতই কঠিন। এ খাতে ডা. জাফরুল্লাহ’র মতো চরিত্রকেও এখন আর বিশেষ দেখা যায় না।
*
ওষুধ নীতির পর দ্বিতীয়বার ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী আক্রান্ত হন স্বাস্থ্য-নীতি তৈরির সময়। ১৯৮৭ সালের মার্চে স্বাস্থ্য-নীতির তৈরির জন্য চার সদস্যের যে কমিটি হয় তাতে ছিলেন তিনি। এই কমিটির প্রধান সুপারিশ ছিল স্বাস্থ্য খাতের বিকেন্দ্রীকরণ। বিশেষ করে চিকিৎসকদের গ্রামে নেয়ার ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাকে একত্রিত করা, স্বাস্থ্য কাঠামোতে জনপ্রতিনিধিদের মতামত প্রকাশের সুযোগ তৈরি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জবাবদিহিতা বাড়াতে অডিট শক্তিশালী করা, রাষ্ট্রীয় মেডিক্যাল কলেজসমূহের শিক্ষকদের প্রাইভেট প্রাকটিস বন্ধ করা এবং তার বদলে তাদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো ইত্যাদি।
১৯৯০-এর অক্টোবরে এই স্বাস্থ্য-নীতি বিল আকারে জাতীয় সংসদে আলোচনার জন ওঠে। ঐ দিনই ডাক্তারদের সংগঠন বিএমএ ‘জনস্বার্থ বিরোধী স্বাস্থ্য-নীতির বিরুদ্ধে’ ৭২ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দেয়। পাশাপাশি তারা ডা. জাফরুল্লাহসহ আরো দুই জনের সদস্যপদ খারিজ করে স্বাস্থ্য-নীতি তৈরিতে যুক্ত থাকায়। ২৭ অক্টোবর গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র আবার ব্যাপকভাবে ভাঙচুর হয়। অংশ বিশেষে আগুন দেয়া হয়।
স্বাস্থ্য-নীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের পাশাপাশি এসময় জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের দাবিতেও দেশে আন্দোলন চলছিল। তারই ফল হিসেবে নব্বুয়ের ডিসেম্বরে এরশাদ পদত্যাগ করেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে দেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। সেই সরকারে অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন বিএমএ’র সভাপতি ডা. এম এ মাজেদ। সরকারের প্রথম দিনই সংসদে প্রস্তাব আকারে থাকা স্বাস্থ্য-নীতি-বিলটি বাতিল হয়। তবে ডা. জাফরুল্লাহ’র বিরুদ্ধে অনেকেরই রাগ-ক্ষোভ তখনও থামেনি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকাকে দিয়ে তাঁকে গ্রেফতারের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হতে থাকে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু হয়। এসময় বিএমএ’র নানান দাবির সমর্থনে এগিয়ে আসতে দেখা যায় ওষুধ শিল্প সমিতিকে।
ওষুধ মালিকদের সঙ্গে চিকিৎসকদের সেই বন্ধন ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এদেশে কেবল শক্তিশালীই হয়েছে। বিপরীতে জনকল্যাণমূলক একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য বিকল্প চেষ্টাগুলো খুব বেশি দাঁড়াতে পারেনি।
*প্রথম প্রকাশিত হয় ‘রাষ্ট্রচিন্তা’ নামক জার্নালে, ২০২১ সালে।